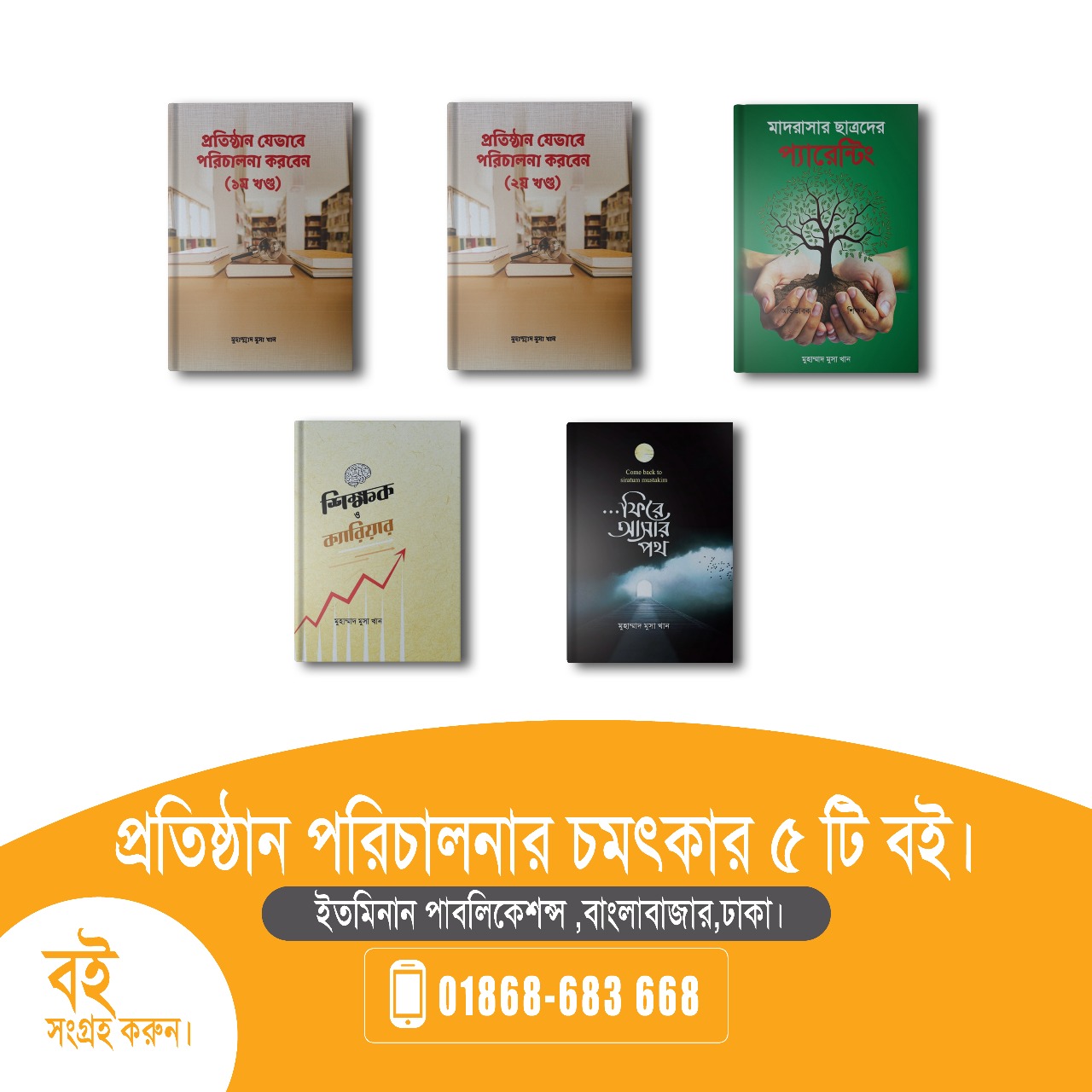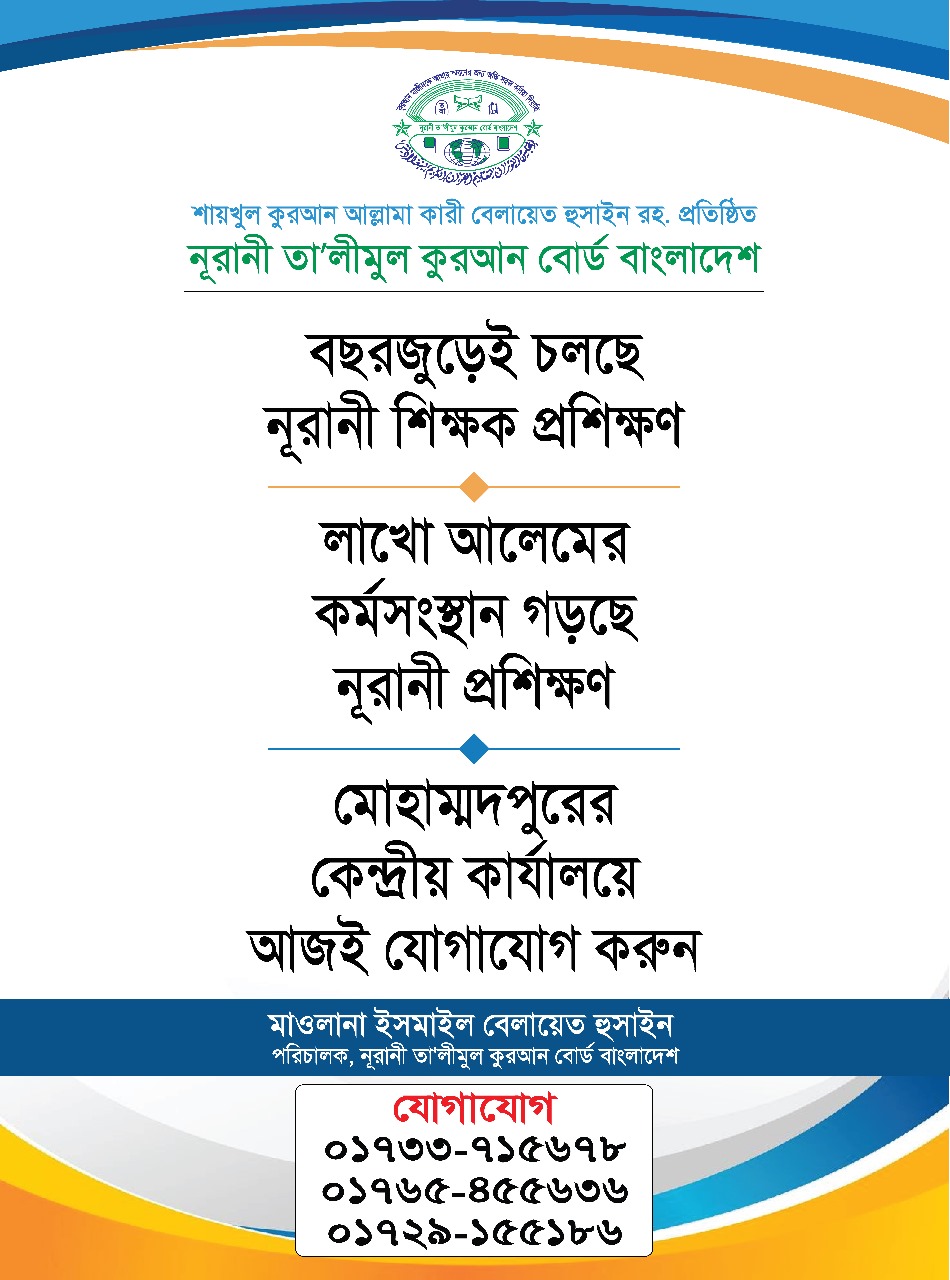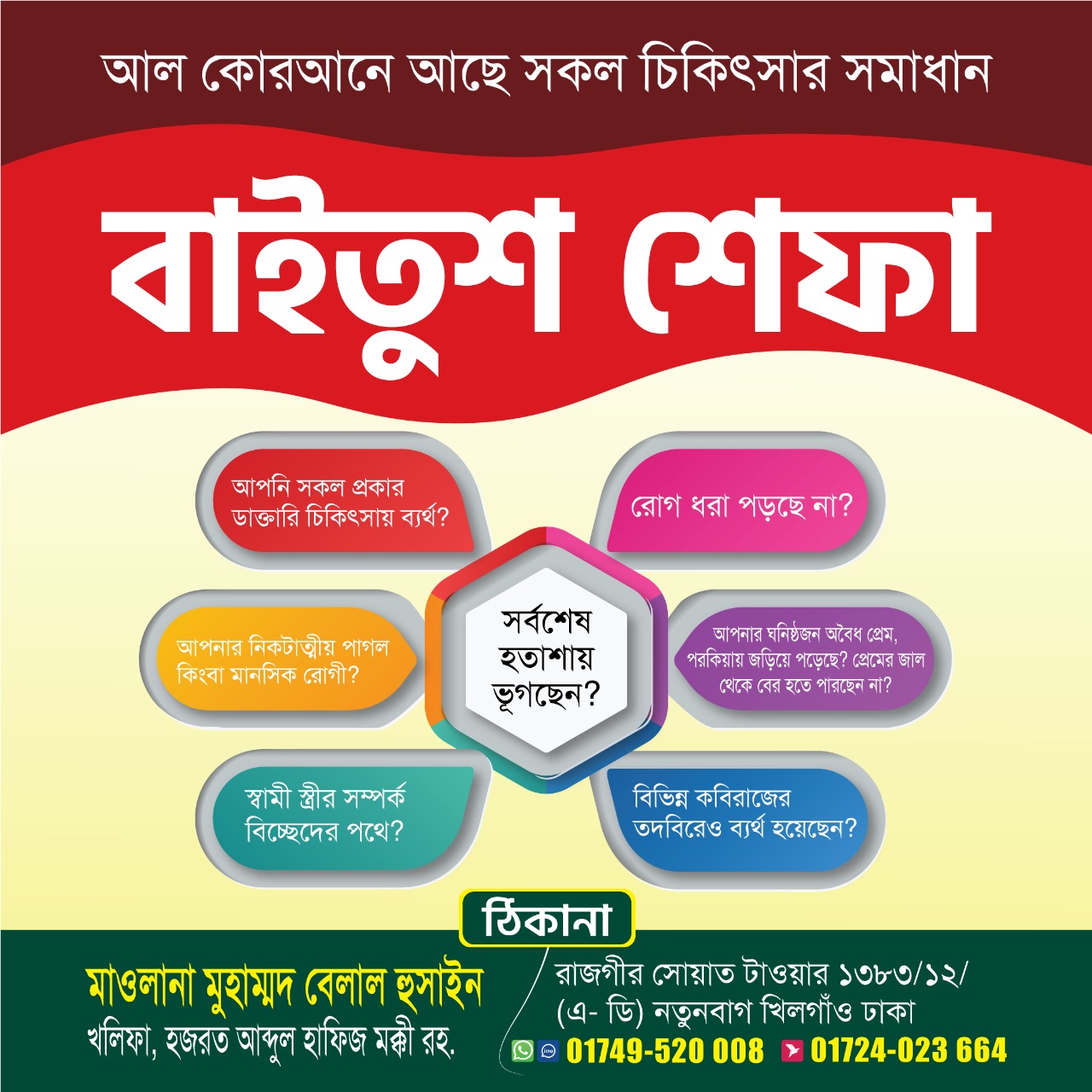আতাউর রহমান খসরু ১৭৫৭ সালে পলাশীর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর এ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন দীর্ঘায়িত করতে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্রিটিশ বেনিয়ারা।
তারই অংশ হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যক্রম শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় সহায়তায় খ্রিষ্টান মিশনগুলো ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্ম সনাতন (হিন্দু) ও ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। বাহ্যত তারা শিক্ষা, চিকিৎসা ও মানবিকতার ধারক হলেও প্রকৃত পক্ষে তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদের বাহক।
খ্রিষ্টান যাজকদের প্রচেষ্টায় তৎকালে অশিক্ষা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে পিষ্ট বহু হিন্দু ও মুসলিম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। খ্রিষ্টান মিশনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মের পক্ষে যেমন রাজা রামমোহন রায় সোচ্চার হয়েছিলেন, তেমনি ইসলাম ধর্মের পক্ষে সোচ্চার হয়েছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ।
অখণ্ড বাংলা, বিহার, আসাম ও ত্রিপুরার মুসলিমদের ঈমান রক্ষা তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তার অনলবর্ষী বক্তৃতা, লিখনি ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তেমনি তিনি ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা বর্ণনা করেছেন।
একই সঙ্গে তিনি পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিমদের কুসংস্কার, অশিক্ষা ও কর্মবিমুখতা থেকে রক্ষা করারও প্রয়াস পেয়েছেন। লেখক মোহাম্মদ আলী চৌধুরী বলেন, ‘বাংলার মুসলিম জাগরণের এমন এক নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী পুরুষ ছিলের মুন্সী মেহেরউল্লাহ্।
দীনহীন অবস্থা থেকে স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টা ও চরিত্রবলে যারা উন্নতির শীর্ষতম শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে অসাধারণ বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক ন্যায়বান পুরুষ। তার মত সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি মুসলমান সমাজে বিরল।’ (মুসলিম বাংলার মনীষা, পৃষ্ঠা ৫৯)
মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ ১৮৬১ সালে যশোরের কালীগঞ্জ উপজেলার ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। পার্শ্ববর্তী ছাতিয়ানতলা গ্রামে ছিল পৈতৃক নিবাস। তার পিতার নাম মুন্সি মুহাম্মদ ওয়ারেস উদ্দিন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটায় তার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বেশি দূর আগায়নি।
তবে তিনি যশোরের মৌলবি মোসহারউদ্দীনের কাছে ধর্মশিক্ষা এবং মৌলবি মোহাম্মদ ইসমাইলের কাছে আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষা লাভ করেন। এ সময় তিনি কুরআন-হাদিস ও ফারসি সাহিত্যেও বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। (বাংলা পিডিয়া, প্রবন্ধ : মেহেরুল্লাহ, মুনশি মোহাম্মদ)
মাত্র ১৪ বছর বয়সে যশোর জেলা বোর্ডে কর্মচারী পদে তার কর্মজীবন শুরু হয়। জনৈক ইংরেজ তাকে দার্জিলিং নিয়ে গেলে সেখানে তিনি ‘মানসুরে মোহাম্মদী’ পত্রিকা এবং ‘খ্রীস্টধর্মের ভ্রষ্টতা’ নামক পুস্তক পড়ার সুযোগ পান। এই পুস্তক পাঠের পর তার ধর্মানুরাগী মন ইসলাম ধর্মের প্রতি আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। (মুসলিম বাংলার মনীষা, পৃষ্ঠা ৬১)
এছাড়াও সোলায়মান ওয়ার্সির ‘কেন আমি আমার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম’ ‘কেন আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলাম’ ও ‘প্রকৃত সত্য কোথায়’ গ্রন্থগুলো তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এরপরই তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দর্জি পেশায় নিয়োজিত হন। খড়কি গ্রামের জাহা বকস মির্জা ছিলেন তার দর্জি বিদ্যার গুরু। তার কাছে পাঁচ-ছয় বছর কাজ শেখার পর যশোর শহরের দড়াটানায় নিজস্ব দোকান চালু করেন। (কাজী শওকত শাহী, প্রবন্ধ : মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ
তৎকালে খ্রিষ্টান যাজকরা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে ঘুরে ঘুরে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করত এবং প্রচলিত হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারও চালাতো। এসব ঘটনা মুনশী মেহের উল্লাহকে ব্যথিত ও বিচলিত করত। প্রথমে তিনি পাদ্রীদের কথার বিপরীতে প্রশ্ন ও প্রতিবাদ করতেন, পরবর্তী সময়ে পাদ্রীদের মতো গ্রামে-গঞ্জে, হাট-বাজারে ঘুরে ঘুরে অপপ্রচারের উত্তর দিতেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতেন।
কথার যুক্তি, বক্তৃতার ধার ও অতুলনীয় বাগ্মিতার কারণে দ্রুতই তিনি বাঙালি মুসলমানের নয়নমনি হয়ে উঠলেন। এ কাজে ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকসহ অসংখ্য মনীষী তাকে স্নেহাশীস দেন। ইসলাম প্রচারে তার প্রধান মাধ্যম ছিল সভা-সমিতি ও জনসমাগমে বক্তৃতা করা এবং দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল লেখালেখি। কথাসাহিত্যক শাহেদ আলী মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লার বক্তৃতার প্রভাব সম্পর্কে সমকালীন একজন কবিকে উদ্ধৃত করেছেন। যে লিখেছেন, ‘নিজের সমাজের দুঃখ কাহিনী বর্ণনার সময় তার বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্মস্থলে গিয়ে বিঁধতো।
এজন্য কত মানুষকে হা হা রবে ক্রন্দন করতে দেখেছি। বাস্তবে তিনি এসেছিলেন অকল্যাণের অবসান ঘটাতে, কাজেই তার বাক্যেও এমন ছিল যা মুসলমান সমাজের জড়তা ভেঙ্গেছে, তাদের চেতনা ফিরিয়েছে, বাংলার অবিস্সৃত মুসলমানের আত্মপলব্ধি করতে শিখেছে, তাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সাধিত হয়েছে, এক কথায়, সমাজ জেগেছে।’ (মুন্সী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা ১৩১)
বক্তৃতার পাশাপাশি তিনি হাতে কলমও তুলে নেন। খ্রিষ্টবাদের অসারতা, খ্রিষ্টান মিশনারির অপপ্রচারের উত্তর, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও সাপ্তাহিক ‘মিহির ও সুধাকর’, মাসিক ‘ইসলাম প্রচারক’-সহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ১৮৯২ সালে ‘খ্রীস্টীয় বান্ধব’ পত্রিকা ধর্মান্তিত খ্রিষ্ট ধর্মপ্রচারক জন জমিরুদ্দীন ‘আসল কোরআন কোথায়?’ শিরোনামে একটি বিভ্রান্তিকর লেখা প্রকাশ করেন।
তাতে তিনি কুরআনের ওপর ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তার প্রশ্নের উত্তরে মুনশী মেহের উল্লাহ সুধাকর পত্রিকায় (১৮৯২ সালের জুন মাসের ২০ ও ২৭ তারিখে) ‘ঈসাই বা খ্রীস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন’ ও ‘আসল কোরআন সর্বত্র’ শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ লেখেন। উত্তর সন্তুষ্ট হয়ে জমিরুদ্দীন ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন এবং মুনশী জমিরুদ্দীন নাম ধারণ করেন। (কাজী শওকত শাহী, প্রবন্ধ : মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ)
গ্রহণযোগ্য সূত্রে মুনশী মেহের উল্লাহ মোট ১২টি গ্রন্থ রচনা করেন। তা হলো খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা, রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলে এছলাম, মেহেরুল এছলাম, সাহেব মুসলমান (অনুবাদ), পান্দেনামা (অনুবাদ), খ্রীষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ, জাওয়াবোন্নাছারা, বাবু ঈশানচন্দ্র ম-ল ও চার্লস ফ্রেন্সের এছলাম গ্রহণ, ঈসাই বা খ্রীস্টানী ধোকা ভঞ্জন, মানব জীবনের কর্ত্তব্য। (মুন্সী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৭-১৮)
তার রচনা সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান লেখেন, ‘রীতি প্রকরণের দিক থেকে যে সমস্ত রচনাকে আমরা সাহিত্য বলি সে ধরনের সাহিত্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচনা করেননি। কিন্তু তিনি যা করেছেন মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় শুদ্ধতার ক্ষেত্রে তা অনন্যসাধারণ।
রাজা রামমোহন রায় যে অর্থে বাঙালী হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আধুনিক জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অর্থে হিন্দু সমাজকে তার চিন্তার দৈন্যদশা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহও তেমনি খৃষ্টান ধর্মের আগ্রাসন থেকে বাঙালী মুসলমানকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন।’ (মুন্সী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা ২০৯)
ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবে বরেণ্য এ মনীষী কখনও কখনও প্রতিপক্ষের সঙ্গে ‘বাহাস’ বা বিতর্কেও লিপ্ত হয়েছেন। ১২২৮ বঙ্গাব্দে ফিরোজপুরে তার জীবনের অন্যতম আলোচিত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই তর্কযুদ্ধে তিনি খ্রিষ্টান মিশনারিদের পরাজিত করেন। ঐতিহাসিক সে বিতর্কের বিবরণ তার ‘খ্রীষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ’ পুস্তিকায় স্থান পেয়েছে। (মুসলিম বাংলার মনীষা, পৃষ্ঠা ৬৬)
কর্মী, সদস্য, পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ একাধিক সভা-সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরমধ্যে কয়েকটি হলো কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন, বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনীয় মুসলমান সমিতি, আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি ইত্যাদি। (মুন্সী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৫)
কর্মজীবনে মুনশী মেহের উল্লাহর একটি সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। তাদের প্রধান ছিলেন কলকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবি ও ফারসির অধ্যাপক মৌলভি মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, কলকাতা আলিয়া মাদরাসার বাংলা সংস্কৃতের অধ্যাপক প-িত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, বাঁশহাটের মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ।
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও বিনম্র। অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তিনি জীবনযাপন করতেন। বিলাস ব্যসনের মোহ তাকে কখনও আকৃষ্ট করতে পারেনি। দরিদ্রের অভাব মোচনের জন্য তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। নিজ বাড়িতে বহু ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার বাড়িটি ছিল একটি ক্ষুদ্র এতিমখানা বিশেষ। উত্তরবঙ্গে একদিনে তিনটি সভা করে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর ক্রমে নিউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়।
এ রোগেই ৭ জুন ১৯০৭ মোতাবেক ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। বৈবাহিক জীবনে দুই স্ত্রীর গর্ভে তিনি তিন ছেলে ও তিন মেয়ের পিতৃত্ব লাভ করেন। (মুসলিম বাংলার মনীষা, পৃষ্ঠা ৬৯)
বর্তমান সময়ে মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে কবি জাকির আবু জাফর বলেন, ‘আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কেন যেন মনে হয় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ একটি গতিশীল ছায়াপথ। মুসলমানদের এমন মুসিবতের সময় আর একজন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ প্রয়োজন।
সঠিক সময়ে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আর একজন নেতা প্রয়োজন। যিনি যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এনজিওর বেড়াজালে মুসলমানদের পা আটকে গেছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বিশ্বাসের উপত্যকা কেটে গেছে। মুসলমানের সন্তান অথচ ভিন্ন ধর্মের কালচার লালন করছে। হায় আফসোস! আজ যদি আবার আসতো একজন মুন্সী মেহেরুল্লাহ।’ (মুন্সী মেহেরউল্লা : জীবন ও কর্ম, পৃষ্ঠা ২০৬)
লেখক: সহসম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ
[লেখা ও লেখকের কথা প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাময়িকী ‘লেখকপত্র’ এর সৌজন্যে]
-এটি